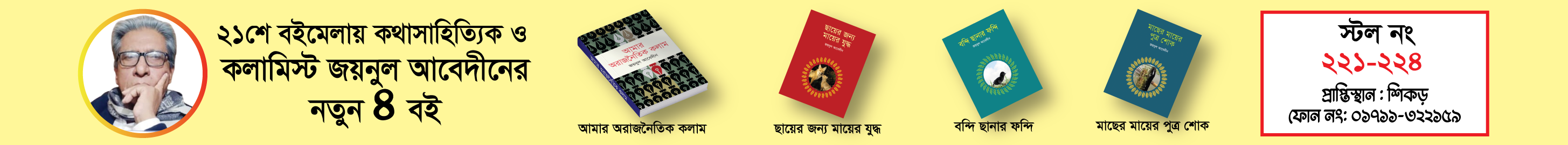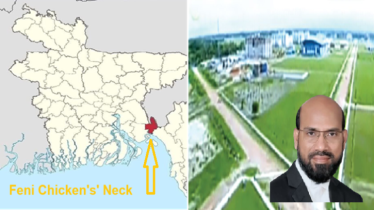অন্তর্বর্তী সরকারেই মুক্তি দেখছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের প্রতীক। একদিকে যেমন এটি একটি দমনমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে এটি একটি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।
বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম একটি সরকার আগে দেখা যায়নি—যা তত্ত্বাবধায়ক বা সেনাসমর্থিত নয় বরং নিখাদভাবে নাগরিক চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
একটি ব্যতিক্রমধর্মী সরকার
মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার বৈশ্বিকভাবে নজিরবিহীন এক উদাহরণ। তিনি একাধারে অর্থনৈতিক দর্শন ও সামাজিক উদ্যোক্তা তত্ত্বের পথপ্রদর্শক, যিনি দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ধারণা দিয়ে বিশ্বজয় করেছেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সরকারে রয়েছে একটি নৈতিক অবস্থান ও আস্থার জায়গা, যা বাংলাদেশে অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলো। দলীয় রাজনীতির গণ্ডির বাইরে থাকা এ সরকার নতুনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে—যেখানে জনসেবা, জবাবদিহিতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।
ইতিবাচক অগ্রগতি
এ সরকার ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা, যানজট নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপ, এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন—এসব প্রাথমিক সাফল্য সরকারের প্রতি জনআস্থাকে বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান, আমলাতান্ত্রিক সংস্কার, এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ একটি কাঠামোগত রূপান্তরের বার্তা বহন করছে। বিশেষত যেখানে পূর্ববর্তী সরকারগুলো রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও ক্ষমতার লোভে এসব কার্যক্রম ব্যর্থ করে তুলেছিলো, সেখানে এ সরকার নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে এগোতে পারছে।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ
বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। একদিকে ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রয়াস, অন্যদিকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও রোহিঙ্গা সংকটের বাস্তবতা; তৃতীয়ত, পশ্চিমা বিশ্বের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন যেমন ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন এবং চীনের সঙ্গে বৈশ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে এক জটিল কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। এ অবস্থায় ইউনূসের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং নেটওয়ার্ক একটি কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে হচ্ছে।
আরও পড়ুন <<>> ভারতে ওয়াকফ বিতর্ক: মসজিদ-মাদ্রাসা কি নিরাপদ?
তড়িঘড়ি নির্বাচনের ঝুঁকি
অনেক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী দ্রুত নির্বাচন চাচ্ছে, যাতে তারা ক্ষমতায় ফিরে যেতে পারে। তবে এমন তড়িঘড়ি নির্বাচন কয়েকটি গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে:
১. সংস্কার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে: বর্তমানে যে প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কার চলছে তা সময়সাপেক্ষ। দ্রুত নির্বাচন হলে এ প্রক্রিয়াগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুনরায় ফিরে আসবে।
২. জনগণের আস্থায় চিড় ধরবে: জনগণ এ সরকারকে একটি ভিন্ন ও পরিচ্ছন্ন বিকল্প হিসেবে দেখছে। যদি সরকার হঠাৎ করে বিদায় নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষ মনে করবে আবারও একটি ‘অর্ধ-পরিবর্তন’ ঘটেছে, যা প্রকৃত অর্থে কিছুই বদলায়নি।
৩. নির্বাচন অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নাও হতে পারে: বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণ, দমনপীড়নের ইতিহাস এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার না হলে আগাম নির্বাচন অনেকে বর্জন করতে পারে বা অংশগ্রহণ সীমিত হবে, যা দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফ্যাসিস্টের রেখে যাওয়া বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়, সেটা বিগত ১৬ বছরে এদেশের জনগণ হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে।
৪. অর্থনীতি ও বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা: রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনির্ধারিত সরকার পরিবর্তন স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। একটি স্থিতিশীল অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারমুখী পরিবেশ গড়ে তুলে অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।
রোডম্যাপ ও রাজনৈতিক ঐকমত্য
বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো একটি সুসংগঠিত ও বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ। এখানে একটি গ্রহণযোগ্য সময়সীমা নির্ধারণ করে, সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ভবিষ্যৎ নির্বাচন আয়োজনের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এ অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত সময় পেলে, প্রয়োজনীয় আইনি, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্ন করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে সক্ষম হবে। তবে নির্বাচন কেন্দ্রিক এবং অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে কিংবা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থায় থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনুস অধিক সম্মানিত হবেন বলেও কথা চাউর আছে।
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এটি কেবল একটি সরকারের পালাবদল নয়, বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতির শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা। তবে এ প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক ঐক্যমত্য এবং জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা যাবে। অতি তড়িঘড়ি নয়, বরং বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই এ সরকার যৌক্তিক সময়ে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে সফল হতে পারে।
লেখক:
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও
রাজনৈতিক বিশ্লেষক।